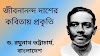কবির লেখনীতে ধরা
পড়েনি এমন কোনো বিষয় দৈনন্দিন জীবনে নেই । তার কাব্যে গল্পে , উপন্যাসে, নাটকে , কবিতায় জীবনের
কথা নানাভাবে নানারূপে আমাদের সামনে হাজির । তাঁর কাব্যনাট্যে পৌরাণিক এবং
মহাভারতীয় নারীদের এনেছেন । বিশ্লেষণ করেছেন নিজস্ব ভঙ্গিমায় । কখনও তা সমাজের
অনুগ হয়েছে কখনো তা আমাদের চোখে একেবারে নিজস্বতা নিয়ে সমাজ দর্শন ও ভাবনার
ভিন্নরূপতা পেয়েছে ।
নান্দী :
গান্ধারীর আবেদন , কর্ণকুন্তী সংবাদ , বিদায় অভিশাপ ও চিত্রাঙ্গদা –
বিশ্বকবি ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুরের এই চারটি নাট্যকাব্য নিয়ে আলোচনা ছোটবেলা থেকেই
শুনে আসছি । বহু প্রবন্ধ পাঠও করেছি । আলোচনাও শুনেছি অসংখ্যবার । এ প্রসঙ্গে
যতবার শুনেছি বা পড়েছি ততবারই কিছু নতুন পাপড়ি খুলে গেছে চোখের সামনে । যা বুঝেছি
, যা ভেবেছি , সবই যে ঠিক , সেই দাবি করছি না । তবে চেষ্টা
করেছি উপলব্ধি যতটা ভেতরে নিয়ে যাওয়া যায় ।
চারটি নাট্যকাব্যে নারী চরিত্র
পাঁচটি : গান্ধারী , কুন্তী , ভানুমতী ( গৌণচরিত্র ) , চিত্রাঙ্গদা ও দেবযানী । এঁদের
মধ্যে গান্ধারী ও কুন্তী এসেছিল মা হয়ে । চিত্রাঙ্গদা ও দেবযানী এসেছিল প্রেমিকা
হয়ে । ভানুমতীর পরিচয় দয়িতা । অবশ্য দয়িতা গান্ধারীও ,এমন কী চিত্রাঙ্গদাও নাট্যকাব্যে পরের দিকে সহধর্মিণী
তথা সহকর্মিণী ।
এই নারী চরিত্রগুলোর প্রতিটিই
নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল । এই পাঁচটি চরিত্রের মধ্যে একটা গভীর যোগসূত্রও
খুঁজে পাওয়া যায় । দেবযানীর চরিত্র প্রেমিকার ,অবুঝ এবং স্বার্থপর মনোভাবাপন্ন । বিপরীতে
চিত্রাঙ্গদা আত্মমর্যাদার পরিপূর্ণতায় ভরপুর । ভানুমতী পুরুষের অধীনতা মেনে
নিয়েই খুশি । কুন্তী জননী হলেও কর্ণের ক্ষেত্রে মায়ের কর্তব্য পালনের দায়িত্ব নিতে
রাজি ছিল না । গান্ধারীও মা কিন্তু তার মাতৃত্ব সার্বজনীন । এমন কী , স্ত্রী হয়ে যে যথার্থ
সহধর্মিণী । কারণ পুত্রস্নেহে অন্ধ দয়িত তার যুক্তিজালে ছিন্ন ক্লিন্ন হয়েছে ।
কুন্তী কেবলমাত্র অর্জুনসহ পঞ্চপাণ্ডবেরই মা । গান্ধারী পাণ্ডব , দ্রৌপদী এবং প্রজাদেরও মা ।
নিজের সন্তান দুর্যোধনের কুশাসন ও অত্যাচার থেকে সে সবাইকে বাঁচাতে চেয়েছিল । সেই
সঙ্গে কঠোর শাস্তি দিয়ে ছেলেকেও শুদ্ধ করতে চেয়েছিল । চিত্রাঙ্গদা যেমন আদর্শ
প্রেমিকা , গান্ধারীও
তেমনি আদর্শ মা । দুজনেই আদর্শ নারীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ।
দেবযানী
দেবযানীর প্রেম ছিল
আত্মকেন্দ্রিক । দেবযানী নিজেকে কচের কাছে খুলে ধরবার পরে কচ যখন জানিয়েছিল— “আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
... " , তখন দেবযানী
উল্লসিত হয়ে উঠেছিল , কচকে সে তখনই প্রস্তাব দিয়েছিল— “ থাকো তবে ...। ” কারণ সে বুঝেছিল । তার প্রেম
ব্যর্থ হয়নি । অবশ্যই কচ প্রতিবাদ করেছিল । কিন্তু দেবযানী তা মানতে চায়নি । কচ
যখন জানাতে চেয়েছিল যে , প্রেমের চেয়েও জাতির প্রতি কর্তব্য অনেক বড় তখন দেবযানী
বলেছিল— “করেনি কি
রমণীর লাগি কোনো নর মহাতপ । ” দেবযানীর বিশ্বাস ছিল যে , জ্ঞান এবং খ্যাতিতে সুখ নেই ।
চেয়েছিল কচ বলুক,দেবতাদের শক্তি বাড়াবার চেয়ে দেবযানীই তার
কাছ বেশি কাম্য ।
দেবযানীকে কচ বোঝাতে চেয়েছিল
যে , তার কাছে
জাতির কল্যাণই ছিল একমাত্র লক্ষ্য । যে প্রতিজ্ঞা করে সে দেবলোক থেকে রওনা হয়েছিল
সেটাই তার মনে সব সময়ে । জাগ্রত ছিল । যুবতী নারীর প্রেম তাকে প্রতিপূরণের পথ
থেকে একটুও সরাতে পারেনি । কচের কথা শুনে দেবযানীর আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল । উল্টে
সে রেগে গিয়েছিল । কচকে সে মিথ্যাবাদী বলেছিল । কচ দেব্যানীর সহায়তায় তার বাবা
শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব পেয়েছিল । আর সেই উদ্দেশ্যেই সে দেবযানীর প্রতি ছদ্ম -
প্রেমের অভিনয় করেছিল — এ - ও ছিল । দেবযানীর অভিযোগ । দেবযানীর প্রেমের চেয়ে
দেবজাতির মঙ্গল অর্থাৎ ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টি কচের কাছে বড় হয়েছিল — দেবযানী তা সহ্য করেনি । কচকে
নিদারুণ অভিশাপ দিয়েছিল ।
দেবযানীর চরিত্রটিতে কবিগুরু
একজন অতি সাধারণ বা Conventional আত্মকেন্দ্রিক নারীকেই একেছিলেন । তার কাছে নারীর
সৌন্দর্য এবং যৌবনই ছিল সবচেয়ে বড় গর্বের বস্তু । সে সবের আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান
করায় এবং দেবযানী তার যে সব উপকার করেছিল , তার বিনিময়ে নিজের প্রতিজ্ঞা
ভুলে যেতে রাজি না হওয়ায় দেবযানী বিরূপ হয়েছিল । প্রত্যাখ্যাত প্রেম তখন
নিদারুণ অভিশাপে পরিণত হয়েছিল । অন্যত্র কবিগুরু লিখেছিলেন “ এ যে তার বাইরের জিনিস , এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে
পাওয়া বর , ক্ষণিক মোহ -
বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য । ” প্রকারান্তরে কবি বলতে
চেয়েছিলেন , যে ওই
বহিরঙ্গ নিয়েই ছিল দেব্যানীর যত অহংকার , যত কামনা।
এখানে বলা দরকার যে মানব সভ্যতা
যতই এগিয়েছে , মানুষের
চিন্তাশক্তির মান ততই আদিমতা ও প্রাচীনতা কাটিয়ে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে । Sex , সে জন্যই অন্তত কিছু মানুষের
হৃদয়ে সৌন্দর্যময় ভালোবাসায় পরিণত হয়েছে । Sex সেখানে বাদ যায়নি । কিন্তু
কেবলমাত্র Sex- ই পুরুষ ও
নারীর সম্পর্কের একমাত্র সেতু হয়ে দাঁড়ায়নি । দেবযানীর মধ্যে এই বোধ ছিল না ।
তাই সে কচের আদর্শকে চূর্ণ করে , কচের গণ্ডীকে ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল ।
নিজের সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধের ক্ষেত্রে পিছুটান হয়ে আসতে চেয়েছিল
তার প্রেম। কচের আদর্শ আর দেবযানীর কামনা পরস্পরের বিরোধী । হয়ে দাঁড়িয়েছিল । রাজা সম্বরণ সূর্যের মেয়ে তপতীকে লাভ করবার
জন্য চরম কষ্টের সাধনা করেছিল — এটি দেবযানীর কাছে ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা ।
কবিগুরু অবশ্য অন্যত্র ব্যর্থ প্রেমের ব্যক্তিত্বকে দিয়ে বলিয়েছিলেন— “ আমার রয়েছে কর্ম । আমার রয়েছে
। বিশ্বলোক । ” কবির মনোভাব সেখানেই
নিহিত রয়ে গেছে ।
চিত্রাঙ্গদা
আদর্শ প্রেমিকার চরিত্র ছিল
চিত্রাঙ্গদা । কবি চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্যের সূচনায় লিখেছিলেন “ যদি ... অন্তরের মধ্যে যথার্থ
চারিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের
পক্ষে মহৎ লাভ , যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায় । ” কবিগুরুর চিত্রাঙ্গদা একজন
যােদ্ধা এবং শাসক ছিল । কিন্তু সে কোন সময়েই প্রেম বাদ দিয়ে sex- কে ভাবতে চায়নি । Sex- কে মোটেও অস্বীকার
করেনি । সেই সঙ্গে প্রেমের জোয়ারেও সে ভেসেছিল , প্রেমিক অর্জুনকেও ভাসিয়েছিল ।
একটি পুরুষ আর একটি নারীর মিলনে ভালোবাসাই সবচেয়ে মহত্তম এবং বৃহত্তম
উপকরণ হতে পারে ; sex আসবে তার পেছনে — এটিই যেন চিত্রাঙ্গদা প্রমাণ
করেছিল । কচের কাছে দেবযানীর নিজেকে প্রকাশ করতে অনেকটাই
ইতস্তত ভাব ছিল । প্রথমে ব্যঙ্গের কটুকথা বলে , তারপরে শুক্রাচার্যের কাছে
শিক্ষালাভের সময়কার নানা ঘটনা বর্ণনা করে , এমন কী হোমধেনু আর নদীর
কথাও তুলে দেবযানী আশা করেছিল , যে কচ সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও কাম্যরূপে তার নামই বলবে । আর
চিত্রাঙ্গদা পুরুষের মতোই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শিকারে
গিয়েছিল । অর্জুনকে দেখেই তার মনে প্রেমের জন্ম হয়েছিল । একদিন পরে সে অনভ্যস্ত
নারীর সাজে অর্জুনের সামনে গিয়েছিল । সরাসরি সে অর্জুনকে বিয়ে করতে চেয়েছিল ।
যেহেতু সে এতকাল পুরুষের মতােই আচার - আচরণ করত তাই । ওই প্রস্তাব দিতে গিয়ে সে
দেবানীর মতাে নানা কথা বলেনি । কারণ তার মনে তখনও লজ্জার স্থান ছিল না । কিন্তু
সম্ভবত কুরূপা এবং নির্লজ্জ বলেই অর্জুন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল—
“ব্রহ্মচারিব্রতধারী আমি । পতিযোগ্য নহি ... ” কচ দেবানীর প্রতি ভালোবাসাকে পুরোপুরি অস্বীকার করেনি । সে জানিয়েছিল— “ চির জীবনের সনে তার নাম গাঁথা হয়ে গেছে । ” এমন কী এও স্বীকার করেছিল— “ আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয় । ” কিন্তু সে এ - ও বলেছিল— “ ধর্ম জানে , প্রতারণা করি নাই । ” কচের ভালোবাসা ছিল সম্ভবত প্লেটোনিক , তার পরিণতি কখনই sex বা বিয়েতে হতে পারত না । অন্যদিকে অর্জুনের প্রত্যাখ্যানের অজুহাতে ব্রহ্মচার্য থাকলেও মূলে ছিল নিশ্চয় চিত্রাঙ্গদার সৌন্দর্যহীনতা এবং নির্লজ্জ ভাব । চিত্রাঙ্গদা এই বিতৃষ্ণাকে দূর করতে চেয়েছিল । চিত্রাঙ্গদার মনে প্রথম থেকেই তিলে তিলে অর্জুনকে জয় করবার ইচ্ছে ছিল । সেই সংগ্রাম অতি সাধারণ নারীর কেবলমাত্র sex— বা রূপ - যৌবন সম্বল হোক , এটা সে চায়নি । কিন্তু ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসীকে দীর্ঘ সময় পাওয়া যাবে । বলে সে নিজের অনভ্যস্ত ও অপছন্দের পথ বেছে নিয়েছিল । সে মদনের সাহায্যে সুন্দরী সেজেছিল । সেই সুন্দরী চিত্রাঙ্গদাকে দেখে অর্জুন ব্রহ্মচর্য থেকে বিচ্যুত হয়েছিল । চিত্রাঙ্গদা সুন্দরী সাজলেও , নিলজ্জের মতো তার কাছে নিজের কামনার মানুষের নাম প্রকাশ করলেও সম্পূর্ণ “ কামিনী ” হতে পারেনি । সে যে অর্জুনের বীরত্বেই মুগ্ধ হয়েছিল , সে এ কথাই প্রকাশ করেছিল । অর্জুন তার প্রেমকে স্বীকৃতি দিলে কিন্তু চিত্রাঙ্গদা খানিকটা হতাশ হয়েছিল । দেহের আকর্ষণে অর্জুন চিত্রাঙ্গদার কাছাকাছি এলে সে বলে । ফেলেছিল— “ কোথায় রহিল পড়ে নারীর সম্মান । কারণ মদনের সহায়তায় পাওয়া দৈহিক সৌন্দর্য তার গুণকে অতিক্রম করে গিয়েছিল । যার জন্য এত পরিকল্পনা তাকেই । সে বলেছিল— “ শৌর্য বীর্য মহত্ব তোমার দিয়ো না মিথ্যার পদে । ”
কিন্তু এখানে কবিগুরু বিচ্ছেদের
চিন্তা আনেন নি । কারণ sex একটি চরম সত্য । যৌন - আকর্ষণের পটভূমিতেই গড়ে ওঠে
আবেগপূর্ণ প্রেম । চিত্রাঙ্গদা — অর্জুনের যৌন জীবন শুরু হয়েছিল চিত্রাঙ্গদা এবং অর্জুনের
পরস্পরের প্রতি দৈহিক আকর্ষণে । কিন্তু চিত্রাঙ্গদা বিশ্বাস করত— “এই ছদ্মরূপিনীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ
আমি শতগুণে । ” অন্যদিকে
অর্জুন নারীদেহ সম্ভোগে ব্যস্ত থাকলেও দস্যুরা রাজ্য আক্রমণ করেছে শুনেই অস্ত্র
নিয়ে তাদের দমন করতে যেতে চেয়েছিল। চিত্রাঙ্গদাও সেই সময়ে তার কর্মসহচরী হতে
চেয়েছিল । কবির নিপুণ তুলিতে এভাবেই দুজনের মধ্যে প্রেমের জন্ম হয়েছিল। এটাই ছিল
চিত্রাঙ্গদার নৰ্মসঙ্গিনী থেকে কর্মসঙ্গিনী তথা জীবনসঙ্গিনীতে রূপান্তরিত হবার
কাহিনি । শেষে চিত্রাঙ্গদা আবার তার পুরুষ - কঠিন অসুন্দর রূপ ফিরে পেয়েছিল ।
কিন্তু তখন অর্জুন আর তাকে প্রত্যাখ্যান করেনি । তাকে পেয়ে “ ধন্য হয়েছে বলে স্বীকার করেছিল
। কারণ চিত্রাঙ্গদা তার বাহ্যিক অসুন্দর রূপ নিয়েও গর্বের সঙ্গে জানিয়েছিল –
নই , অবহেলা করি
পুষিয়া রাখিবে
পিছে , সেও আমি নহি ।
যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সংকটের পথে ; দূরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও ,যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব
সহায় হইতে ,
যদি সুখে দুঃখে মোর
কর সহচরী ,
আমার পাইবে
পরিচয় । ”
যুবক - যুবতীরা পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হবে — এটাই স্বাভাবিক । ব্রহ্মচর্য কিংবা কামহীনতা বাস্তবে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী । আবার শুধুমাত্র sex , যে কোনো দম্পতিকে পশুর পর্যায়ে নিয়ে যায় । সেই সঙ্গে এও বলা হয় যে , দয়িত ও দয়িতা দুটি অর্ধাংশ , যা মিলে । হয় একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ । কবিগুরু এই সম্পর্কে তার বক্তব্য পরিষ্কার করে এই দুটি নাট্যকাব্যতে বলেছিলেন। দেবযানীর প্রেমের ব্যর্থতা দেবযানীর প্রতি বেদনা জাগালেও কচের প্রতিই কবির সম্পূর্ণ সমর্থন প্রকাশ পেয়েছিল । অন্যদিকে চিত্রাঙ্গদার sex- সর্বস্বতা কাটিয়ে ওঠা এবং মহত্বর ও উন্নততর জীবনের পাদদেশে পৌঁছে যাওয়াও তার কাম্য ছিল বোঝা যায় ।
দয়িতা ভানুমতী , চিত্রাঙ্গদা ও গান্ধারী
ভানুমতী অত্যন্ত অল্প সময়ের
জন্য এলেও বিশ্বকবির একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি । সাধারণ পুরুষেরা যখন দয়িত হয় , তখন ধরে নেয় , যে তার দয়িতার অস্তিত্বের কারণ
( raison
d'etra) সে এবং একমাত্র সে । এটাও বিস্ময়কর যে অধিকাংশ দয়িতাও
সেটাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে । নারী ও পুরুষের সিংহভাগই মনে করে বিবাহিতা নারীর
অবশ্য কর্তব্য । দয়িতকেই তুষ্ট করা । কাজেই দুর্বল এবং ক্ষমতাহীনরূপে দেখা হয়
বলেই পরিবারে ও সমাজে নারীর স্বাতন্ত্র ও মর্যাদা হয় খুবই কম । নারীও যুগ যুগ ধরে
তা মেনে নিতে নিতে আরও বেশি পায়ের তলায় চলে যাচ্ছে । ভানুমতী ওই পুরুষ
নির্ভরতারই একটি জ্বলন্ত চিত্র । আজ যখন Women's lib আন্দোলন যথেষ্ট দানা বেঁধেছে , তখনও কিন্তু ভানুমতী অধিকাংশ
বিবাহিতা নারীর প্রতিনিধিত্ব করে চলেছে ।
শঠতা ও অন্যায় আচরণের মধ্য
দিয়ে পাওয়া দয়িতের জয়কে সে আনন্দদায়ক মনে । করেছিল । পাণ্ডবেরা নানা রাজ্য
জয় করে দ্রৌপদীকে যত গয়না আর মূল্যবান পোশাক উপহার দিয়েছিল , বনবাসে যাবার সময়ে দ্রৌপদী তার
সবই ফেলে গিয়েছিল । ভানুমতী সেই সব পরে নিজেকে গর্বিত ও আনন্দিত মনে করেছিল ।
কারণ দয়িতের কাজের সমালোচনা করার অধিকার কোন দয়িতার আছে বলে সে মনেই করত না ।
গান্ধারী ভানুমতীকে দুর্যোধনের
অন্যায়ের পরিণাম সম্পর্কে সচেতন করতে চাইলে , সে পুরুষশাসিত সমাজের অতি
সাধারণ একজন নারীর মতই জানিয়েছিল— “ দুর্ভাগ্যের ভয় নাহি করি । ” ক্ষত্রিয় পুরুষেরা সেই যুগে
জয় - পরাজয় তথা জীবন - মৃত্যুকে পাশে রেখেই চলত । তাদের দয়িতারাও একই সঙ্গে সুখ
- আনন্দ - গৌরব এবং দুঃখ - বেদনা - অসম্মানকে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিত ।
পুরুষশাসিত সমাজের শিক্ষা অনুযায়ী ভানুমতী সেই জীবন নিয়ে বাঁচতে যেমন জানত , মরতেও তার জানা ছিল বলে ঘোষণা
করেছিল । অর্থাৎ দুর্যোধন যে পথে যাবে ভানুমতীও সেই রাস্তাতেই হাঁটবে — কোন তর্ক বা প্রতিবাদ ছাড়াই — এই ছিল তার মানসিক গঠন ।
এর পাশাপাশি চিত্রাঙ্গদা
অর্জুনকে যা বলেছিল , তা দেখা যাক । সে দাম্পত্য জীবনের সব সময়েই , সব পদক্ষেপেই , সমস্ত কাজেই অর্জুনের সমান
মর্যাদার সঙ্গী হতে চেয়েছিল । সে better half হতেও চায়নি , অর্জুনকে worse half -এ পরিণত করবারও চেষ্টা করেনি ।
তার দাবি ছিল সমান অর্ধাংশ হবার। অর্জুন এবং তার সবসময়েই সমান অধিকার থাকবে , এই ছিল তার আন্তরিক ইচ্ছা ।
অন্যদিকে গান্ধারীর মুখোমুখি
হবার ভয়ে দুর্যোধন পালিয়ে গিয়েছিল । ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর কঠোর ও যুক্তিযুক্ত
সমালোচনায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল , বলতে বাধ্য হয়েছিল— “ সংহর সংহর তব বাণী। ” নারীর মর্যাদা রক্ষা করা
ক্ষত্রিয়ের তথা মানুষের ধর্ম । কিন্তু দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময়ে ধৃতরাষ্ট্র তো
বটেই অন্যান্য অভিজাত যোদ্ধারাও কোন প্রতিবাদ করেনি । গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্র এবং
তাদের সবাইকে দোষী প্রমাণ করে ধিক্কার দিয়েছিল— “ পৌরুষ কোথায় গেছে ছাড়িয়া
ভারত।” এই ধিক্কার
প্রমাণ করেছিল যে গান্ধারী পুরুষনির্ভর ভানুমতী ছিল না । তার মধ্যে ব্যক্তিস্বাতবোধ
অটুট ছিল । পুরুষপ্রধান সমাজেও সে পুরুষকে কাঠগড়ায় তুলতে ইতস্তত করেনি । মর্যাদা
হারিয়েছিল ভানুমতী । কিন্তু তার মানসিক গঠন তাকে তাতেই আনন্দিত করেছিল ।
গান্ধারীর মধ্যে মর্যাদাবোধ প্রবল ছিল ।। তাই নারীর অসম্মান সে সহ্য করতে পারেনি ।
পুরুষেরা মূক থাকলেও সে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল । সুতরাং নারী স্বাধীনতার এক
চিরকালীন উদাহরণ এই কাব্যনাট্যের গান্ধারী ।
দয়িতকে বাদ দিয়ে ভারতীয়
নারীর কোন পরিচয় থাকে না , এই প্রচলিত সত্যকে গান্ধারী বাতিল করেছিল । তার পরিচয়
ধৃতরাষ্ট্রের দয়িতারূপে নয় , লাঞ্ছিত নারী সমাজের একজন প্রতিবাদী প্রতিনিধিরূপে , যার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে জর্জরিত
হয়েছিল ধৃতরাষ্ট্র তথা নির্বাক অপরাধী পুরুষ সমাজ ।
কুন্তী
কুন্তীর পরিচয় পেয়ে কর্ণ তাকে “ অর্জুনজননী ” বলে সম্বোধন করেছিল । নাট্যকাব্যের শেষেও তার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে কর্ণ তাকে কেবলমাত্র ওই পঞ্চপাণ্ডবের মা বলেই চিহ্নিত করেছিল । কুন্তীর কাতরতা সত্ত্বেও পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ হবার প্রলোভন এবং মর্যাদা লাভের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে কর্ণ ঘোষণা করেছিল— “সূতপুত্র আমি , রাধা মোর মাতা । ” সেইসময়ে কুন্তীর আক্ষেপেও কিন্তু ছিল কর্ণেরই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি । কুন্তী চিন্তিত হয়েছিল এই ভেবে যে , জন্মের পরেই পরিত্যক্ত শিশু মহাযোদ্ধা হয়ে ফিরে এসে কুন্তীর পাণ্ডব - ছেলেদের দিকেই অস্ত্র নিক্ষেপ করবে । উদ্দেশ্য কুন্তীর যাই থাক না কেন , ওই সাক্ষাৎকারের পরেই কর্ণের মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছিল ।
কর্ণের পরিচয় প্রকাশ করতে
গিয়ে কুন্তীর মধ্যে বার বার লজ্জা প্রকাশ পেয়েছিল । এতে কোন সন্দেহই নেই , যে কৌরব - পাণ্ডবদের
অস্ত্রপরীক্ষার আসরে কর্ণের আবির্ভাব থেকে শুরু করে বার বার কর্ণের পরিচয় প্রকাশ
করবার সুযোগ আসলেও কুণ্ডী লজ্জাতেই তা প্রকাশ করতে পারেনি। এমনকী , যুদ্ধের আগে কর্ণের
প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও কুন্তী যদি সর্বসমক্ষে কর্ণের পরিচয় এবং নিজের মাতৃত্ব
স্বীকার করে নিত , তাহলে
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সম্ভবত ঘটতই । সেক্ষেত্রে বহু অকালমৃত্যু এবং শোক ও বিয়োগব্যথা
এড়ানো যেত । মহাভারতে আছে , কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর কুন্তী কর্ণের পরিচয় প্রকাশ করেছিল
। তখন পাণ্ডবদের আফশোস করা ছাড়া আর কিছুই করবার ছিল না ।
কুন্তী কর্ণকে বলেছিল— “ তোমারে বসাব মোর সর্বপুত্র
আগে..কর্ণের উত্তর ছিল । সুচিন্তিত এবং যুক্তিনির্ভর । যারা সব হারিয়েছে , সেই পাণ্ডবদের কাছ থেকে
মাতৃস্নেহের ভাগ নিতে কর্ণ অসম্মতি জানিয়েছিল । তাছাড়া কর্ণ জানত যে , মাতৃস্নেহ জোর করে পাওয়া যান না।
তবুও কর্ণ কুন্তীকে স্বীকৃতি
দিয়েছিল । বলেছিল— “তোমার দক্ষিণ
হস্ত ললাটে চিবুকে রাখো ক্ষণকাল”। এমনকী পরিচয় প্রকাশের আগে কুন্তীকে পরম শত্রু “ অর্জুনজননী ” জেনেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল — পৌরুষ ও ধর্ম ছাড়া কুন্তীর
প্রার্থিত সবই সে দিতে প্রস্তুত । তা সত্ত্বেও কর্ণ কিন্তু কুন্তীর থেকে মানসিক
দূরত্ব বজায় রেখেছিল । প্রথমেই “অর্জুনজননী ” সম্বোধন করে এবং পরে “ রাজমাতা ” বলে , তাকে ত্যাগ করবার কারণ জানতে
চেয়েছিল । এর সামান্য পরেই কুণ্ডীর কাতরতা দেখে উদারহৃদয় কর্ণ প্রশ্নটি
প্রত্যাহার করেছিল ।
কর্ণের এই আচরণ কুন্তীকে কর্ণের
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য করেছিল । কুন্তী তখন যা বলেছিল , তাতেই প্রকাশ পেয়েছিল কুন্তীর
মানসিক গঠন । কর্ণকে সে জানিয়েছিল যে , (মাতৃস্নেহ দিতে নয় ) কর্ণকে সে পাণ্ডবদের পক্ষেই নিয়ে
যেতে এসেছিল । জ্ঞানে হোক , অজ্ঞানে হোক , কুণ্ডীর পাণ্ডব - মুখীনতা এখানেও প্রকট হয়েছিল ।
যদিও বিশ্বকবি কুন্তীর চরিত্রে
সরাসরি স্বার্থপরতা আরোপ করেননি , কিন্তু বিশ্লেষণে বিয়োগব্যথাবিধুরা মা কুন্তীর আড়ালে
স্বার্থপরতা চোখে পড়ে বই কী । বাস্তবে কুন্তীর আকুলতা , ক্ষমাপ্রার্থনা এবং অনুশোচনা
সত্ত্বেও পাণ্ডবপক্ষেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল । মাতৃত্ব যে স্তরে উঠলে নৈতিক
ও সার্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করে , কুন্তী সেই স্তরে উঠতে পারেনি । দেবযানীর পাশাপাশি যেমন কচ
উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল , এখানেও তেমনি কর্ণই ত্যাগ ও আদর্শের বিচারে পাঠকের পছন্দের
চরিত্র হয়ে উঠেছে ।
বিশ্বকবির এই নাট্যকাব্যে
ট্রাজিক রস স্মরণীয় হয়েছে । কুন্তী যৌবনে লজ্জার বশে একটি অন্যায় করেছিল । তার
পরেও লজ্জায় তা প্রকাশ করতে পারেনি । অথচ ওই যুগে ক্ষেত্রজ সন্তান স্বীকৃতি পেত ।
পাণ্ডবেরা সবাই নিয়োগ প্রথারই ফসল । কংসের জন্মও স্বাভাবিকভাবে হয়নি । সে যুগে কানীন
সন্তান অবহেলা পেত না বা তার মা বিতাড়িত হত বলেই মনে হয় । কুন্তীর ওই ভুলই
কুণ্ডীর ট্রাজেডি । আর সেই ভুলই কর্ণের মৃত্যু নিশ্চিত করেছিল । ওইখানেই বিশ্বকবি
নৈতিক ও সার্বজনীন মায়ের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছিলেন পাঠকের সামনে ।
কুন্তী যে কর্ণকে কাছে টেনে
নিতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিল — এর জন্য সে - ই দায়ী । কারণ সে সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে
পারেনি । তার নিজের আবেগ এবং অনুভূতি আহত হবার জন্যও সে - ই দায়ী । তার চেতনা এবং
মূল্যবোেধ তাকে ভুল পথে চালনা করেছিল — এর জন্যও সে - ই অপরাধী । বিভিন্ন সময়ে তার পছন্দ , সিদ্ধান্ত এবং কাজের দায়ও তারই
। সে দুঃখ পেয়েছিল তার নিজের ভুল কাজের জন্যই । তার জীবন কর্ণের ব্যাপারে
বেদনাময় হয়েছিল , এও তার নিজের
অবদান । কর্ণের প্রতি তার মাতৃত্বকে সে নিজেই ব্যর্থ করে দিয়েছিল ।
পরোক্ষে কুন্তীর আচরণ আরও একটি
চরম সত্য প্রকাশ করেছিল । নারী শৈশবে জন্মদাতা বা পালকের , যৌবনে দয়িতের এবং বার্ধক্যে
ছেলের অধীন এটাই ভারতীয় সমাজে প্রচলিত রয়েছে। কুন্তী কর্ণের মা হওয়া সত্ত্বেও
নিজের অপ্রকাশিত লজ্জার অতীত । তথা কর্ণের পরিচয় কর্ণের কাছে প্রকাশ করে
পাণ্ডবদের জয়যাত্রার পথই পরিষ্কার করেছিল । আড়ালে থেকেও সে পাণ্ডবদের বিজয় -
রথের যাত্রাপথ মসৃণ করেছিল । ভানুমতীর মতই এটিও প্রায় পুরুষের প্রয়োজনে নিজেকে
উৎসর্গ করা । কুন্তী যেন এক অদৃশ্য প্রচলিত প্রথার শেকলে বাঁধা ছিল ।
অনন্যা গান্ধারী
গান্ধারীর মধ্যে বিশ্বকবি একজন
মা বা একজন দয়িতা কিংবা একজন অসাধারণ । নাগরিককেই তুলে ধরেননি । তিনি গান্ধারীর
মধ্য দিয়ে একজন সচেতন ও প্রতিবাদী আদর্শ নারীকে প্রকাশ করেছিলেন । গান্ধারী
দুর্যোধনের মা হলেও তার অন্যায় আচরণকে সহ করেনি । ধৃতরাষ্ট্রের কাছে দুর্যোধনকে
ত্যাগ করবার অনুরোধ জানিয়েছিল । ছলনা করে । কেড়ে নেওয়া রাজ্য ( ইন্দ্রপ্রস্থ )
যাতে সে কোনভাবেই ভোগ করতে না পারে , সেই ব্যবস্থা । করবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল । পাণ্ডবদের মতো
দুর্যোধনকেও নির্বাসন দণ্ড দেবার সুপারিশ করেছিল ।
এ দাবি গান্ধারী করেছিল
দুর্যোধনের প্রতি বিদ্বেষবশত নয় , তার ক্ষমার অযোগ্য অন্যায় । আচরণের জন্য । এই দাবি জানাবার
সময়ে গান্ধারীর মনে অন্যের তুলনায় অনেক বেশি । ব্যথার জন্ম হয়েছিল , কিন্তু তবুও সে স্নেহের বশে
অন্যায়কে সমর্থন করেনি , চুপ করে থাকেনি । যুধিষ্ঠিরকে আশীর্বাদ করেছিল ।
মানবতাবাদের একটি অসামান্য অবদান ছিল এই বিস্তৃত মাতৃত্ব । সেই মাতৃত্ব নিজের
গর্ভের সন্তান আর অন্যের সন্তানকে একই চোখে । দেখতে শিখিয়েছিল । যে ন্যায়ের
পক্ষে তাকেই সমর্থন রবার পথ দেখিয়েছিল । নিজের গর্ভের সন্তান অন্যায় করলে
নিরপেক্ষভাবে বিচার করে তার বিরোধিতায় সোচ্চার হওয়ার মতো শক্তি জুগিয়েছিল ।
বিশ্বকবির গান্ধারীর মধ্যে এই বিস্তৃত মাতৃত্বকেই চিনে নেওয়া যায় অতি সহজেই ।
এমনকী , এ জাতীয়
মাতৃত্ব সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকলেও সমস্ত পাঠকেরই গান্ধারীকে পছন্দ হয় । নারী
হলে গান্ধারীর মতো হবার ইচ্ছা জাগে।
গান্ধারী বাস্তবসচেতন ছিল ।
ধৃতরাষ্ট্রকে সে ধর্মের পথে চলবার পরামর্শ দিয়েছিল । সেইসঙ্গে জানিয়েছিল যে ধর্ম
তাকে “ দুঃখ নব নবই
দেবে । জানিয়েছিল যে , ধর্মের পথ । ধরে চললে সুখ বা সম্পদ কোনটাই পাওয়া যাবে না ।
কিন্তু যে বা যারা আদৌ কোন অন্যায় করেও নিঃস্ব হয়েছিল , তাদের রাজ্য কেড়ে নিয়ে যে
অপরাধ করা হয়েছে , দুর্যোধনকেও
বনবাসে পাঠিয়ে নিজে দুঃখ পেয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে
বলেছিল । গান্ধারী । তাহলে দুর্যোধনের অন্যায়কে যেমন দণ্ডিত করা হবে , তেমনি পাণ্ডবদের প্রতি শঠতা ও
দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার সময়ে চুপ করে থাকায় যে অপরাধ হয়েছিল তার জন্যও কিছুটা শাস্তিভোগ
করা হবে । গান্ধারী পুত্রবধু ভানুমতী ভুল পথে চলছিল দেখে তাকেও সদুপদেশ দিয়েছিল ।
গান্ধারীর মধ্যে সবচেয়ে
লক্ষণীয় যা ছিল , তা হচ্ছে তার
বিশ্লেষণ ক্ষমতা । দুর্যোধন যখন বিজয় উল্লাসে মত্ত , সেই সময়ে গান্ধারী বলেছিল— “কৌরবকল্যাণ লক্ষ্মী অত্যাচারে
প্রতীক্ষিছে বিদায়ের ক্ষণ রাত্রিদিন ” । এই তাৎক্ষণিক জয়ের সূত্র ধরেই যে ধ্বংস আসছে , তা গান্ধারী অনুমান করেছিল ।
দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার পরিণতি কী হতে পারে , তাও সে বুঝেছিল । বহুদিন ধরে যে দুর্যোধনের সম্পর্কে
মানুষের মুখে ধিক্কার ধ্বনিত হবে , সেই ভবিষ্যৎবাণীও গান্ধারী করেছিল।
কুন্তীর স্নেহ ছিল পাণ্ডবদের প্রতি । কর্ণের প্রতিও তার ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছিল । কিন্তু নিজের সন্তানদের বাইরে তা ছড়িয়ে পড়েনি । গান্ধারীর ভালোবাসা কৌরবদের ছাপিয়ে পাণ্ডবদের প্রতিও বর্ষিত হয়েছিল । গান্ধারী পুরুষের অনুগামিনী ছিল না । তাকে দেখেই বোঝা গিয়েছিল— “ আকাশের আধখানা তুমি নারী । ”
দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার জন্য
গান্ধারী গোটা অভিজাত সমাজকেই দায়ী করেছিল । গান্ধারী তখন মা ছিল না , ছিল না দয়িতা । সে তখন
নারীজাতির প্রতিভূরূপে নিজের বক্তব্য জানিয়েছিল । তার দাবি ছিল— “ সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন । ” সুবিচার না পেয়ে গান্ধারী
বুঝতে পেরেছিল যে , অত্যাচারের
ভয়াবহ পরিণাম এড়ানো যাবে না । সেদিন ভয়ংকর ত্রাসের দিনকে সহজভাবে নেবার জন্য
গান্ধারী শান্তভাবে অপেক্ষা করবার সংকল্প গ্রহণ করেছিল । আত্মধিক্কারে বিষন্ন
গান্ধারী কুরুকুলের সমস্ত নারীর আসন্ন দুঃখের কল্পনায় ব্যথিত হয়েছিল । বাস্তবে
নারীনির্যাতনকারী কাপুরুষকে সে বিন্দুমাত্র সমর্থনও করতে পারেনি । তার সমর্থন ও
আশীর্বাদ ছিল নির্যাতিত পক্ষের জন্যই । অপমানিত দ্রৌপদীর প্রতিই ছিল তার সহানুভূতি
ও সমর্থন ।
উপসংহার
বিভিন্ন সময়ে চিন্তার বিকাশ
ঘটায় উন্নততর , মার্জিততর
আরও অগ্রসর চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন সাহিত্যিকেরা । বিশ্বকবির গান্ধারী চরিত্র তারই
একটা উদাহরণ । মহাভারতের গান্ধারীর মধ্যে কবি অনেক নতুনত্ব আরোপ করেছিলেন । ফলে ওই
চরিত্রটি মানবতাবাদী । চিন্তার উজ্জ্বলতম উদাহরণে পরিণত হয়েছিল । কুন্তীর বিপরীতে
গান্ধারীকে রাখলে এই বৈপরীত্য আরও ভালো বোঝা যায় ।
এই নাট্যকাব্যগুলো লেখবার সময়ে
স্রষ্টার কী উদ্দেশ্য ছিল তা জানি না । কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই চারটি
নাট্যকাব্যে তিনি প্রেমিকা , দয়িতা এবং মায়ের একটি করে আদর্শ তুলে ধরেছিলেন । একটা কথা
অবশ্য বলা দরকার যে , আজ আমরা নারী - স্বাধীনতা প্রসঙ্গে যতখানি অগ্রসর হতে
পেরেছি , বিশ্বকবির
সময়ে ততখানি এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি । কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
যে পথে বিচরণ করেছিলেন , বিশ্বকবি ঠিক সেই পথে সেভাবে যাননি । সেটার কারণ তার
সামাজিক অবস্থান তথা পরিবেশ । কবির ‘ যোগাযোগ উপন্যাসের নায়িকা বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে
। ওই যুগে ওই চরিত্র ঠাকুর - পরিবারের একজন সদস্যের হাতেই সৃষ্টি হয়েছিল । ওই
নায়িকার নারীত্ব , পছন্দ -
অপছন্দ , শিক্ষার
প্রতিফলন এটাই প্রমাণ করে যে কবির মনে নানা প্রশ্ন জেগেছিল এবং সেগুলোর সম্ভাব্য
উত্তরও তিনি তৈরি করেছিলেন । কুমুদিনী কোন মতেই সাধারণ মেয়ে নয় । কিংবা
মঞ্জুলিকা — সে - ও তো
খড়ির গণ্ডী পেরিয়ে যেতে পেরেছিল ।
এটা পরিষ্কার যে কবি বুঝেছিলেন , “ জীর্ণ - পুরাতনকে প্রয়োজন মতো
ভাসিয়ে দিতে হয় , আবাহন করতে
হয় নব পত্রপল্লবকে । যুগে যুগে সমাজ পাল্টায় , সমস্যা পাল্টায় , মানুষের মানসিকতারও পরিবর্তন
হয় । এক যুগের চরম অগ্রসর মতবাদ ও সংস্কার পরের যুগে পশ্চাৎপদ হয়ে বাতিলের দলে
পড়তেই পারে । কারণ তখন আর সেই মূল্যবোধ এগিয়ে যাবার পথ দেখাতে পারে না । সেই
জন্যই “ পশ্চাতের আমি
” চিরকালই বর্তমানের দ্বারা বর্জিত
হয় । আর সত্য তো চরম হতে পারে না । যুগ বদলালে তারও ধারণা বদলে । যায় । কাজেই
বিশ্বকবি তার বিরাট প্রতিভা এবং তার সমকালীন দর্শন তথা মতবাদ এবং উজ্জ্বল
ব্যক্তিত্বদের সান্নিধ্যকে কীভাবে প্রয়োগ করেছিলেন এবং তার সৃষ্টি কীভাবে কতখানি ।
সেই যুগের সামাজিক চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল , সেটা বিচারের সময়ে “ মানুষ ” তাঁকে ভুললে চলবে না । যেমন , ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করবার
জন্য রামমোহন রায় একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন । বিশ্বকবি তারই প্রতিষ্ঠিত
ধর্মমতের অনুসারী হওয়ায় তার । মধ্যেও ধর্মীয় কুপ্রভাব থেকে মুক্তিলাভের একটা
প্রচেষ্টা সব সময়েই দেখা গিয়েছিল । এই কারণেই তার গান্ধারী ধর্ম বলতে
মানবধর্মকেই বুঝেছিল।
দেবযানী শুক্রাচার্যের মেয়ে ।
পরিবেশ তার গৌরবময় । শিক্ষাও অবশ্যই সে পেয়েছিল । কিন্তু সে একেবারে নিম্নস্তরের
মানসিকতা প্রকাশ করে ফেলেছিল । তার মধ্যে নারীত্বের । মর্যাদাবোধ আদৌ প্রকাশিত
হয়নি । কচের প্রতি ব্যাঙ্গোক্তি , কাতর আবেদন , স্বার্থপর প্রস্তাব এবং শেষে কচের সম্মতি না পেয়ে রেগে
যাওয়া , তার অবস্থান
অনেক নীচে নামিয়ে দিয়েছিল ।
পক্ষান্তরে চিত্রাঙ্গদা
অর্জুনের জীবনে স্থায়ী আসন লাভ করেছিল , যদিও তার প্রেমের প্রথম প্রকাশ
কমেই হয়েছিল । কিন্তু সে কামকেই একমাত্র কাম্য ভাবেনি । অর্জুনকে বুঝিয়ে
দিয়েছিল যে , তার অবস্থান
অর্জুনের পাশাপাশি একই গুরুত্বে ।
এরই পাশাপাশি ভানুমতী যেন
দেবযানীরই পূর্ণতা পাওয়া রূপ । তার পরিবেশ ও শিক্ষা তাকে পশ্চাৎমুখী মানসিকতাই
দিয়েছিল । সে জানত তার ভাগ্য পুরুষের ভাগ্যের সঙ্গেই অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবধ।
বিশ্বকবি দুই মায়ের চরিত্রে
কুণ্ডী ও গান্ধারীকে নিয়ে এসেছিলেন । একজন ট্রাজিক রস সৃষ্টি করেছিল । দ্বিতীয়
জন পাঠককে সঠিক পথের নির্দেশ দিয়েছিল । [ বিশ্বকবি ঘরে বাইরে এবং চার অধ্যায় লিখবার
জন্য এখনও সমালোচিত হন । ] তিনি ধর্মকে নস্যাৎ করেননি । কিন্তু মানবতবাদীর মতোই
গান্ধারীকে প্রতিবাদী করে এঁকেছিলেন । বিশ্বকবির বিপুল সৃষ্টিতে কালো মেঘ আছে ।
কিন্তু রূপপালি রেখাও আছে প্রচুর । সেই রূপোলী রেখারই দুটি
চিহ্ন চিত্রাঙ্গদা এবং গান্ধারীর আবেদন । তাঁর উত্তরসূরীরা তাকে সম্যক উপলব্ধি করে
যদি আরও অগ্রসর চিত্রাঙ্গদা ও গাছারী চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন , তাহলেই সমাজ এগিয়ে যাবে , মুক্ত হবে জঞ্জালের দুর্গন্ধ
থেকে ।
বিশেষ দ্রষ্টব্য -
বহু প্রবন্ধকার ও বক্তার প্রভাব
এ প্রবন্ধে আছে । আলাদা করে নাম করতে না পারার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী ।
লেখক পরিচিতি -
তরুণকুমার দে নরেন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক কলেজের পদার্থ
বিজ্ঞানের স্নাতক।পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রনিকস অ্যাণ্ড টেলি-কম্যুনিকেশন বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং বায়োলজিক্যাল এফেক্টস অব ইলেকট্রিক অ্যাণ্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডসে পি এইচ ডি অর্জন করেছেন।
তিনি প্রায় তিন দশক ধরে সাধারণ মানুষের কাছে বাংলাভাষায় প্রযুক্তির তথ্য পরিবেশন করছেন, যে প্রচেষ্টার একটি ফসল তাঁর ‘অজানা
দূষণ’ গ্রন্থ।
যাত্রার বিশিষ্ট
পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র কনিষ্ঠ পুত্র। ছেলেবেলা থেকেই গল্প, প্রবন্ধ ও নাট্যজাতীয়
রচনায় আগ্রহী।
প্রকাশিত গ্রন্থ : বধূ বিনোদিনী, অজানা দূষণ, পালাকার
অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ, পালাকার
ব্রজেন্দ্রকুমার দে, যাত্রা নাটক
প্রসঙ্গ, প্রসঙ্গ :
ব্রজেন্দ্রকুমার দে।
অভিনীত যাত্রাপালা: বধূ বিনোদিনী, সুলতান মামুদ, চাঁদ সদাগর, নসীব, আলোর সারথি (ব্রজেন্দ্র-জীবনী)।