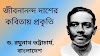ভগিনী নিবেদিতা
-
সাহিত্য রসিক
“হে মহাপ্রাণ, ওঠো, জাগো, জগৎ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতেছে,
তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস আমরা আহ্বান করতে থাকি – যতক্ষণ পর্যন্ত নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত
না হন, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের দেবতা এই আহ্বানে সাড়ানা দেন। জীবনে ইহা অপেক্ষা বড়
আর কি আছে; ইহা অপেক্ষা আর কোন কাজ ... আমি
কোন পরিকল্পনা করিনা। কাজ শুরু করিলে কার্যপ্রণালী আপনি গড়িয়া ওঠে। আমি শুধু বলি জাগো
জাগো”। এই আগ্নেয় পত্রের লেখক হলেন স্বামীজী এবং এটি লিখেছিলেন ৭ই জুন, ১৮৯৬ তারিখে,
আয়ারল্যান্ড দুহিতা মার্গারেটের উদ্দেশে।
১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজি ফিরলেন ভারতে। এসময় মার্গারেটও আসার জন্য স্বামীজির কাছে অনুমতি চান। জানান যে, প্রাণ দিয়ে ভারতবর্ষের সেবা করতে চান তিনি। প্রতি উত্তরে স্বামীজি জানালেন, ‘ঝাঁপ দেওয়ার আগে ভাল করে ভেবে দেখ। যদি কাজে নামার পর ব্যর্থ হও, বা যদি বিরক্তি আসে, তবে আমার দিক থেকে অবশ্যই জেনো আমি আমরণ তোমার পাশে থাকব। তুমি ভারতবর্ষের জন্য কাজ করো বা নাই করো।’
মনস্থির করে ফেললেন মার্গারেট, যাবেন তিনি ভারতে। প্রতীক্ষায়
রইলেন, কবে ডাকেন স্বামীজি। অবশেষে এলো স্বামীজির আশ্বাস: ‘ভারতবর্ষের সেবার জন্য,
কাজের জন্য পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রয়োজন বেশি, যে হবে একজন সিংহী। ভারত এখনও মহীয়সী
নারীর জন্ম দিতে পারেনি। তাই বিদেশ থেকে ধার নিতে হচ্ছে। তোমার শিক্ষা, পবিত্রতা, অসীম
ধৈর্য, দৃঢ়তা ও প্রীতি তোমাকে উপযুক্ত নারী রূপে গঠন করেছে। এদেশের দুঃখ, কুসংস্কার,
জাতিভেদ, ছোঁয়াছুঁয়ি সম্বন্ধে তুমি ধারণা করতে পারবে না...যদি সব কিছু উপেক্ষা করে
এগিয়ে আসতে পার, তবে স্বাগত।’
এমন সাবধান বাণী সত্ত্বেও সাত সাগর পেরিয়ে মার্গারেট এলেন ভারতবর্ষকে অন্তর থেকে ভালবেসে। ১৮৯৭ সালের শেষের দিকে ‘মোম্বাসা’ জাহাজে লন্ডন থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন । এরপর ২৮শে জানুয়ারি ১৮৯৮ সালে নতুন জীবনের স্বপ্ন নিয়ে কলকাতার মাটিতে পা রাখেন মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল।
প্রথম দিকে নিবেদিতা বাংলা জানতেন না বলে শ্রী শ্রী মায়ের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তায় গোঁড়ার দিকে একটু অসুবিধা হলেও শ্রী শ্রী মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে অসুবিধে হত বলে নিবেদিতা বাংলা শেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। প্রথম প্রথম বাংলা শেখার পর নিবেদিতা বাংলা বলতেন অত্যন্ত থেমে থেমে, যত্ন করে। তাঁর বাংলা শুনে শ্রীশ্রী মা খুব হাসতেন, বলতেন নিবেদিতার বাংলা বেদের সময়ের। আসলে নিবেদিতা সাধু-বাংলায় কথা বলতেন।
ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন তখনকার দিনে ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রভাবশালী মহিলাদের মধ্যে অন্যতম। তারুণ্যে ভরা ধর্মযাজকের দুহিতা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল ভারতবর্ষে এসে হয়ে গিয়েছিলেন আমাদের সকলের অত্যন্ত প্রিয় ভগিনী নিবেদিতা। তিনি ভারতবর্ষকে ও তার সমাজ সংস্কৃতিকে প্রাণদিয়ে ভালবেসে ফেলেছিলেন। এ ভালবাসার মধ্যে কোন খাদ ছিল না। উত্তর আয়ারল্যান্ডের ডানগ্যানন শহরে ১৮৬৭ সালের ২৮শে অক্টোবরে তাঁর জন্ম। মাত্র দশ বছর বয়সেই পিতা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবেলকে হারিয়ে মা মেরী ইসাবেলের সাথে মাতামহ হ্যামিলটনের কাছে চলে যান। লন্ডনের এই বোর্ডিং স্কুল থেকে তাঁর বিদ্যালয়ের পাঠক্রম শেষ করেন। এককালের তীক্ষ্ণ মেধাবী ছাত্রী, প্রথাগত পাঠক্রমের বাইরেও প্রচুর আগ্রহ সহকারে সাহিত্য, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, কলাবিদ্যা ইত্যাদি নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে শিক্ষয়িত্রী এবং একজন প্রতিভাময়ী লেখিকা হিসেবে লন্ডনের বুদ্ধিজীবী-মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।
১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে লন্ডনের ‘ওয়েস্ট-এন্ড’-এর এক অভিজাত পরিবারের বাড়িতে এক সন্ধ্যায় ভারতীয় হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ-র ‘বেদান্ত দর্শন’ নিয়ে এক আলোচনায় তিনিও আমন্ত্রিত এক শ্রোতা হিসেবে ছিলেন। এই দিনটি ছিল মার্গারেটের জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। সেদিন স্বামী বিবেকানন্দ-র বেদান্তের অদ্বৈত-তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও ব্যক্তিত্বে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। খুঁজে পান জীবনের এক নতুন পথ। কোনও ধর্মই ছোট নয়, মানবতাই ধর্ম আর এই ধর্মের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। এই উপলব্ধি তাঁকে এক নতুন আলোর পথ দেখায়।
১৮৯৮ সালের ১১ই মার্চ কলকাতার স্টার থিয়েটার-এ এক জনসভায়
স্বামী বিবেকানন্দ মার্গারেট-কে জনসাধারণের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ১৮৯৮ সালের ২৫শে
মার্চ-এর এক সকালে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষা দিয়ে নতুন নামকরণ
করেন – নিবেদিতা। সেদিন গুরু তাঁকে নির্দেশ
দিলেন, আজীবন কঠোর সংযম অবলম্বন করতে আর বুদ্ধের মত মানবসেবায় আত্মোৎসর্গ করতে। পরবর্তী
জীবনে ভারতের সেবাই ছিল তাঁর একমাত্র ধর্ম। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতবর্ষের কল্যাণেই
জগতের কল্যাণ হবে। সেই-সঙ্গে জাগল ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তরের টান, ভালবাসা।
৫ই জুন আলমোড়া থেকে বন্ধু এরিক হ্যামন্ডকে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তাতে এই দিনটিকে তাঁর
‘নিউ বার্থ ডে’ বলে উল্লেখ করেছিলেন, আর উল্লসিত হয়ে বন্ধু নেলকে জানালেন – ‘নোবেল,
ভারতবর্ষ হল প্রকৃতই একটি পুণ্যভূমি, আমার জীবনের স্বপ্ন হল ভারতবর্ষ এবং ইংলন্ডকে
ভালবাসার বন্ধনে এক করে রাখা’।
ভারতের বুকে ১৮৯৮ সাল ছিল নিবেদিতার প্রথম বর্ষ। এই বছরেই তাঁর সাথে আলাপ হয়, ভারতের বিশেষ করে তথা বাংলার স্বনামধন্য অনেক মহাপুরুষের। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কথামৃতকার শ্রীম, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু, তাঁর স্ত্রী লেডি অবলা বসু প্রমুখের সাথে।
ভারতের পুনরুত্থানের জন্য বিজ্ঞানচর্চাকে স্বামীজী অনেক
গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন বলেই গুরুজীর কাজ মনে করেই নিবেদিতা বিজ্ঞান গবেষণার বাধা দূর
করার জন্য জগদীশচন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কারণ সেই সময়ে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র
বসু-কে পরাধীন ভারতবর্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছিল। পৃথিবী
বিখ্যাত বিজ্ঞান প্রতিভার প্রতি পদেই অসহনীয় লাঞ্ছনা সহ্য করতে হচ্ছিল। সেই সময়ের বিদেশের
বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকরা পরাধীন দেশের এই বৈজ্ঞানিককে নিজেদের সমান মর্যাদা দিতে মোটেই
রাজি হননি। তিনি পাননি বিদেশি সরকারের কোনও সহায়তা, ন্যায্য সম্মান। প্রতি পদে তাঁকে
কাজ করতে হয়েছে নানা উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, আর্থিক অনটনের ভেতর। নিবেদিতার মনে হয়েছিল,
বিজ্ঞান-পাগল এই আত্মভোলা মানুষটির পাশে দাঁড়ানো তাঁর পবিত্র জাতীয় কর্তব্য। তাঁকে
ভারতের ‘ জাতীয় সম্পদ’ বলেই মনে করতেন। নিবেদিতা বয়সে তাঁর চেয়ে প্রায় দশ বছরের ছোট
ছিলেন কিন্তু দিনে দিনে এই মানুষটি হয়ে উঠেছিলেন একাধারে তাঁর বন্ধু ও সন্তান। আত্মভোলা
এই বৈজ্ঞানিককে মাতৃস্নেহ দিয়ে সন্তানের মত ভালবাসতেন। শুধু তাই নয়, আদর করে তাঁকে
‘খোকা’ বলে ডাকতেন। নিবেদিতার বহু চিঠিতেই তার উল্লেখ পাওয়া যায়।
১৮৯৮ সালের নভেম্বর মাসে তিনি কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয়
স্থাপন করেন। এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি নানা মানব-কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।
সকল বর্ণের ভারতীয় নারীর জীবনযাত্রার উন্নতির লক্ষ্যে তিনি কাজ শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ
ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসুও তাঁর স্ত্রী অবলা বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ওকাকুরা কাকুজো
প্রমুখ তৎকালীন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছিলেন নিবেদিতার বন্ধু-স্থানীয়। রবীন্দ্রনাথ
তাঁকে "লোকমাতা" আখ্যা দেন। ভারতীয় শিল্পকলার সমঝদার নিবেদিতা ভারতের আধুনিক
চিত্রকলার সৃজনে অন্যতম অনুপ্রেরণার কাজ করেন। নন্দলাল বসু এই কথা একাধিকবার স্মরণ
করেছেন। জীবনের শেষ পর্বে নিবেদিতা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের-সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।
শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা স্থাপিত হয়। কলেজে পড়া কালীন বিভূতি চৌধুরীর একটি
বই-এ পড়েছিলাম যে সিস্টার নিবেদিতা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বোমা তৈরির ফর্মুলা
বিদেশ থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বই ‘মাতৃরূপা
কালী’ পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘ভারত মাতা’ ছবিটি এঁকেছিলেন।
নিবেদিতার সেই সংগ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী অসিতানন্দ
জানিয়েছেন –“তখনকার হিন্দু সমাজ বাড়ির মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোয় উৎসাহী ছিল না। নিবেদিতা
খালি পায়ে পথ হেঁটে, বাড়ি-বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের ধরতেন, যাতে তাঁরা বাড়ির মেয়েদের স্কুলে
পাঠান। ওদিকে রক্ষণশীল পরিবারের লোকেরা ম্লেচ্ছ অহিন্দুর সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করত
না। নিবেদিতার অপূর্ব ভালবাসায় এই বাধাও ক্রমে দূর হল।”
তাঁর এই সাফল্যের মূলে ছিল নিষ্ঠা ও ভালবাসা। সগর্বে ও
সানন্দে নিজের পরিচয় দিতেন তিনি, ‘আমি একজন শিক্ষয়িত্রী।’
শিক্ষিকা নিবেদিতার শিক্ষা পদ্ধতি ছিল সত্যই অভিনব। ছাত্র-ছাত্রীদের
সৃজনীশক্তির প্রতি গুরুত্ব দিতেন, জাগিয়ে তুলতেন ভারতীয় আধ্যাত্ম-প্রাণসত্তাকে। নিবেদিতার
শিক্ষানীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, শিক্ষাকে তিনি সর্ব শ্রেণির
মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। মানব-কল্যাণমুখী এই শিক্ষাদর্শ তাঁর সময়কালকে
পেরিয়ে বর্তমান অস্থির সময়েও তাই অনুসরণ যোগ্য।
১৯১১ সালে পুজোর ছুটিতে শারীরকে ভাল করবার আশায় জগদীশচন্দ্র
বসু পরিবারের সাথে দার্জিলিং যান নিবেদিতা। কিন্তু সেখানে আরও অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী
হয়ে পড়েন। লেডী বসু এবং জগদীশচন্দ্রের অক্লান্ত চেষ্টা স্বত্বেও ‘ভারতের নিবেদিতা’
মাত্র ৪৪ বছর বয়সে ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন। নিবেদিতার স্বপ্ন ছিল একটি বিজ্ঞান মন্দির
গড়ে তোলার। তাঁর পরলোক গমনের পর এই বিজ্ঞান মন্দির গড়ে জগদীশচন্দ্র বসু, নিবেদিতার
সেই একান্ত ইচ্ছা পূরণ করলেন। সিস্টার নিবেদিতা আজও আমাদের ভারতবাসীদের মনে অমর হয়ে
আছেন এবং থাকবেন তার এই সেবামূলক কার্যকলাপের জন্য।
সূত্র – দেশ বিদেশের পত্র-পত্রিকা।